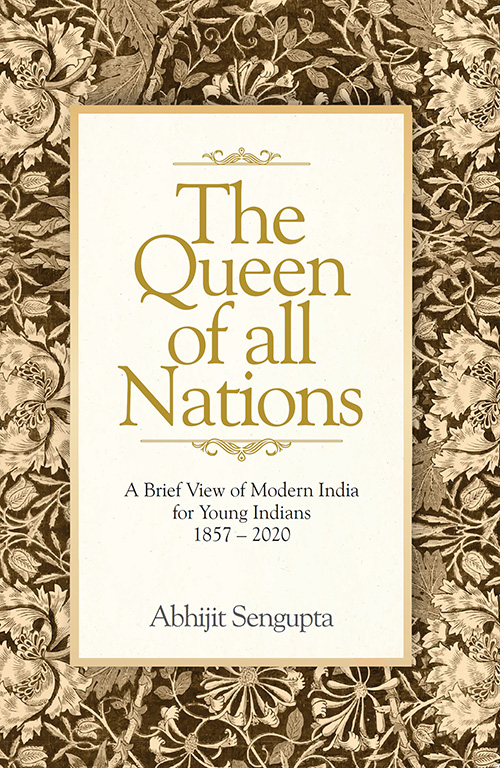জরুরি অবস্থা (Emergency) ঘোষণার দিনটার স্মৃতি এখন ইষৎ ঝাপসা। সেই ঝাপসা স্মৃতির কাচ থেকে ধুলো সরিয়ে এটুকু বলতে পারি ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থার জন্য ক্ষমা চাইলেন আমাদের মনে হয়েছিল, ইতিহাসের এক দুঃসহ অধ্যায়ের অবসান হল। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এর পুনরাবৃত্তি আর কখনও হবে না। ৪৬ বছর পেরিয়ে এসে আজ বুঝতে পারি, আমরা ভুল ভেবেছিলাম। জরুরি অবস্থার ভূত আমাদের আজও প্রতি পল অনুপলে আবার তাড়া করছে, মাত্রাটা স্রেফ আলাদা। সেদিনের জরুরি অবস্থা যদি গণতন্ত্রে কুঠারাঘাত হয়, তবে আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতি গণতন্ত্রের অবিরল রক্তক্ষরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এক কথায় বললে, এই পরিস্থিতিটা অনেক বেশি সাংঘাতিক, এর ফলও দীর্ঘমেয়াদি।
জরুরি অবস্থা সুশাসন শব্দটিকেই বিকৃত করেছিল। সেই সময় সাংসদ পিজি মাভলঙ্কার এই পরিস্থিতিকে সাংবিধানিক স্বৈরাচার বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সুকৌশলে সংবিধানের ৩৫২ নং ধারাটি ব্যবহার করে জরুরি অবস্থা প্রণয়ন করেন। নির্বিচারে কম-বেশি ৫৯ জন সাংসদকে রাতারাতি জেলে ভরা হয়। অন্যান্য বিরোধী নেতা, সাংবাদিকরাও রেহাই পাননি। সংবাদমাধ্যম হকচকিয়ে ওঠে। গোটা বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা হয়েছিল সেবার। নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য একাধিক সাংবিধানিক সংশোধনী খাঁড়ার মতো নেমে আসতে দেখেছি। বলতে পারি, জাতীয় জীবনে জরুরি অবস্থা ছিল একটা অতি বিরল ঘটনা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম চিরদিন এমন যাবে না। আমরা স্বাভাবিকতায় ফিরতে পারব। কিন্তু আজ স্বাভাবিকতা আর জরুরি অবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান সেটাই ঘুচে গিয়েছে। বিরুদ্ধতাকে ছেঁটে ফেলে আর তেলা মাথায় তেল দিয়ে এক নতুন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যখন আছড়ে পড়ছে কেন্দ্রের নেতারা একদল ছুটলেন মহাসমারোহে ভোটের প্রচারে, আরেকদল মাতলেন নানা হিন্দু উৎসব পালনে। হাসপাতালগুলিতে তখন অক্সিজেনের জন্য হাহাকার, কিন্তু জয়ের নেশায় মত্ত শাসকের কানে সেই কান্নার ধ্বনি পৌঁছয়নি। এমনকি ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়েও এক নাগাড়ে গড়িমসি চলেছে। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার ভাবল, বিরুদ্ধস্বর দমন করতে হবে সবার আগে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। প্রশাসনের রক্তচক্ষু মানুষের ক্রোধকে ভয়ে রূপান্তরিত করল নিমেষেই। আর আমরা দেখলাম মিথ্যেগুলিকে কেমন জনতার আবেগ বলে চালিয়ে দেওয়া হল। সকলেই কম বেশি বুঝল মোদির অঙ্গুলিহেলনে ছাড়া সরকার কোনও কাজই করবে না। একই সঙ্গে বোঝা গেল যখনই মোদি-শাহ জুটি চাইবে ঠিক তখনই ব্রাজিল, হাঙ্গেরি, ফিলিপিনস, তুরস্কের মতো নির্বাচিত সরকারের স্বৈরাচারের মডেলটা অনুকরণ করা যাবে।
জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল খানিকটা তাড়াহুড়ো করে। রাজনৈতিক ঐতিহাসিকরা বলেন, ইন্দিরা স্বয়ং বিষয়টা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন কিন্তু সঞ্জয় গান্ধী এবং পারিবারিক আত্মীয়-বন্ধুর চাপেই শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। জরুরি অবস্থা প্রণয়নের প্রতিটি পদক্ষেপে তাই প্রশাসনিক তাড়াহুড়োর চিহ্ন ছিল। রাতারাতি ইন্দিরা বিরোধীদের জেলে ভরা শুরু হয়। নির্মম অত্যাচারে শিউরে উঠেছিল নাগরিক সমাজ। সেদিন রাস্তায় নেমে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের মূল্য দিতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ইন্দিরা জমানা ছাড়া প্রতিবাদের এমন মূল্য দিতে হয়নি ভারতবাসীকে। কিন্তু এই পুরো ঘটনার মধ্যে আদর্শগত প্রস্তুতি ছিল খুব সামান্য। বরং বলা যায়, জরুরি অবস্থার লক্ষ্য ছিল দেশকে দেশবাসীকে রাজনীতিচ্যুত করা। জরুরি অবস্থা জারির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড সঞ্জয় গান্ধী এরপরে দ্রুতই বলে দিলেন রাজনীতি তাঁকে আর আগের মতো টানছে না।
জরুরি অবস্থার যদি কোন আদর্শগত নীতি থেকেও থাকে তা সীমাবদ্ধ ছিল শূন্যগর্ভ ২০টি নীতিতে এবং ৫ দফা পরিকল্পনায়। এর পাশাপাশি এমন একটা কল্পলোক তৈরি করার চেষ্টা চলছিল যেখানে মনে হবে গোটা জাতির স্বরূপ প্রতি মুহূর্তে যেন ইন্দিরা গান্ধীতেই উদ্ভাসিত হচ্ছে। কারও কারও স্মৃতিতে হয়তো থাকবে, ১৯৭৪ সালে জরুরি অবস্থা জারির ঠিক আগে কংগ্রেস নেতা দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছিলেন, ইন্দিরাই ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াই ইন্দিরা। আর এখানেই তাদের ছাপিয়ে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ জুটির ডবল ইঞ্জিন সরকার। মোদি-শাহের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতিকে সামনে রেখে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের রাজনৈতিক স্বৈরাচারের দিকে চোখ রাখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে ফাঁকটা কোথায় ছিল। মোদি শাহের কর্মকাণ্ড এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যা আসলে ভারতীয় জনতা পার্টির পিতৃপ্রতিম সংস্থা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-র আদর্শগত রূপরেখার বাস্তবায়নের অংশ। জরুরি অবস্থার অর্ধশতক আগে অর্থাৎ ১৯২৫ সাল থেকে বহু ধর্মীয় ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রকল্পটি ধীর লয়ে এগোচ্ছিল।
এই লেখাটি লিখতে শুরু করে মনে হচ্ছে, জওহরলাল নেহরুকে অপছন্দের তালিকায় রাখলেও তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তত অপছন্দ করেন না । কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রাজনৈতিক চরিত্রে বেশ কিছু মিল রয়েছে। ব্যক্তিত্বের ক্যারিশ্মাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে তাঁরা নিজেদের দল সাংসদ এবং ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীদের থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছেন। জরুরি অবস্থা জারি করার পিছনে ইন্দিরার ভূমিকা অনস্বীকার্য, কিন্তু তিনি একাই বিষয়টির চালিকাশক্তি ছিলেন এমনটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। তার ছেলে সঞ্জয় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সামনে থেকে কাজ করেছিলেন। ২৯ বছর বয়সি সঞ্জয়ের সে যাবৎ একমাত্র কৃতিত্ব ছিল জনতার গাড়ি তৈরির সরকারি চুক্তি বাতিল করা। সরকারি সংস্থা থেকে বরাত সরিয়ে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া এবং সেই বেসরকারি সংস্থাকে ঋণ ভর্তুকি পাইয়ে দেওয়া।
১ নম্বর আকবর রোডের এই যুবকের বাসস্থানই ছিল সেদিনের ক্ষমতার আসল ভরকেন্দ্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনতার মধ্যে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে পুত্রের নির্দেশ কার্যকর করেছেন মা। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সেদিন ইন্দিরা প্রশাসনের মূল উদ্ভাবন ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ এবং নির্বাচিত মন্ত্রীদের পাশ কাটিয়ে প্রসাদান্নভোগী আমলা ও পুলিশকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করা। এক কথায় বললে ইন্দিরা-সঞ্জয় মিলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে শাসনতান্ত্রিক স্বৈরাচারে পরিণত করেছিলেন। ইন্দিরা যা বলবেন কংগ্রেস পার্টি তাই পালন করবে, রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল এমনটাই। ১৯৭১ সালে বিপুল জনাদেশে ক্ষমতায় ফিরে আসেন ইন্দিরা। ওই বছরেই ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। এই সময়ে ইন্দিরা আরও লোকপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সময়েই দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়েছিল। ইন্দিরা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ বা বিরোধীদের চাপে বোবা পুতুল না হয়ে থেকে তিনি দেশ থেকে গরিবি হঠাবেন।
মোদি-জামানার সঙ্গে ইন্দিরার জামানার কিছু অবিশ্বাস্য মিল রয়েছে। মোদি জামানাতে বহু এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় এমনকি সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীও জানতে পারেন না কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে। ধরা যাক নোটবন্দির কথা। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে তা কি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আগেভাগে জানতেন! বলা যায় তালে তাল দেওয়া মন্ত্রীদের অনেকটা জনসংযোগ কর্তা (PRO) বানিয়ে রাখা হয়েছে এই আমলে। আসলে সরকার চালান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অলটার ইগো। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরই নাম খাতা থেকে বাদ পড়ে। অনেক সময় বহু অযোগ্য লোকও তাদের জায়গা নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে রঘুরাম রাজনের প্রতি বর্তমান শাসকের ব্যবহারের কথা মনে করা যেতে পারে।
জরুরি অবস্থার সময়েও আমরা দেখেছিলাম দক্ষ প্রশাসক নয়, সরকার চাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলা সং। ইতিহাসই যেন মঞ্চ বদলে পুনরায় অভিনীত হচ্ছে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে আমরা দেখি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অজয় ভাল্লা দেশের প্রধান বিচারপতি শরদ এ বোবদেকে বিশ্বের সবথেকে বড় সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক পরিযান সম্পর্কে সরকারি মত জানাতে গিয়ে বলছেন, হাইওয়েতে একজনও পরিযায়ী শ্রমিক নেই। তবে হ্যাঁ জরুরি অবস্থার সঙ্গে আজকের পরিস্থিতি তুলনা করলে এটাও বলতে হবে প্রশাসনিক পদকে ক্ষমতার দাস করে রাখার ক্ষেত্রে সরকারের হাত অনেক লম্বা হয়েছে। যে সব সংস্থাগুলি জন্মলগ্ন থেকে কোনও রকম রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ, তারাই আজ মোদি-শাহের সহযোগী এবং হিন্দুত্ব প্রজেক্টের অংশ হয়ে উঠেছে যেন। নির্বাচন কমিশন, দেশের সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা কন্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) সর্বত্র একই ছবি।
বলাই বাহুল্য নাগরিক সমাজের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার খর্ব করার মধ্য দিয়েই জরুরি অবস্থা তার দাঁত নখ বের করেছিল। ইন্দিরার বিশ্বস্ত উপদেষ্টা পি এন হাসকর আদর্শগতভাবে 'দায়বদ্ধ' বিচারব্যবস্থা এবং প্রসাদান্নভোগী আমলাদেরকেই প্রাধান্য দিতেন। বর্তমান অবস্থাটার দিকে যদি চোখ রাখি দেখব মিডিয়া, বিচার বিভাগ বা রাজনৈতিক দল আপাত সকলেই মুক্ত, কোনও বেড়ি নেই কারও পায়ে। কিন্তু অবস্থাটা এমনই, যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও মুহূর্তে দেশদ্রোহিতা বা অন্যান্য তর্কসাপেক্ষ আইনের আওতায় পড়ে যেতে পারেন। অনেকটা মিসার (মেইনটেনেন্স অব ইন্টারনাল সিকিওরিটি অ্যাক্ট) মতোই নিজেকে প্রমাণের কোনও সুযোগই দেবে না রাষ্ট্র। খুব বুঝেশুনে অপরাধী বাছাই করা হয় এখন, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। ৮৩ বছর বয়সি স্ট্যান স্বামী প্রয়োজনে জলের বোতলটুকুও পান না। ইউএপিএ অনেকটা মিসার মতোই, সরকারের হাতে যখন তখন গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই আইনে। এর পাশাপাশি সরকার ঔপনিবেশিক সময়ের দেশদ্রোহিতা আইন ব্যবহার করছে ইচ্ছে মতো। মিডিয়া নাম নিয়ে এক কলের পুতুল এবং প্রোপাগান্ডা সিস্টেমে এই আইনের গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের সহজেই অ্যান্টি ন্যাশনাল দাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সরকার এই ধরনে অভিযুক্তকে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা না দেওয়ার শিলমোহরও আদায় করে ফেলে।
কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতিতে এসবই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। একথা স্বীকার করে নিতে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার এমন একটি অস্ত্র যার দুইটি প্রান্ত ধারালো। অর্থাৎ সাম্প্রতিক সময়ে যেমন হিন্দুত্ববাদ প্রচার ও প্রসারে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছে তেমনই সরকারের নীতিমালা নিয়ে বারংবার সাহসী সমালোচনা উঠে এসেছে এই মাধ্যমেই। ঠিক এই কারণেই ভিন্নমতকে দমন করার জন্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে মানতেই হবে বিজেপির আইটি সেল কিন্তু প্রতিবাদীদের থেকে অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াকে ‘ব্যবহার’ করেছে। সম্বিত পাত্রের মিথ্যে টুলকিট হোক অথবা বিরোধীদের প্রকাশ্যে অপমান করা, এসবের মঞ্চ হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো জুড়ি নেই। এমনকি একজন অভিযুক্তকে অবমাননার গল্পগুলো রংদার করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেমন দিন কয়েক আগেই নাতাশা নারওয়াল যখন তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না, সোশ্যাল মিডিয়া বারংবার দেখাতে থাকল, এটাই প্রতিবাদের শাস্তি, সরকার সম্পর্কে ভয় জাগিয়ে রাখার রাখার বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে।
স্মৃতিতে আসছে ইন্দিরা আমলের অশ্লীল দমন-পীড়নের নানা কাহন। সঞ্জয় গান্ধীর পাখির চোখ ছিল নগরীর সৌন্দর্যায়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই দুটি বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য প্রচার চালিয়ে ছিলেন দরিদ্র এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে। এই প্রচারপর্ব শেষ হতেই সামনে এল মৃত্যু আর বুলেট বৃষ্টির অভিজ্ঞান। দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটির তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান জগমোহন সঞ্জয়কে এই সময় সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তুর্কমান গেটে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা নিশ্চয়ই অনেকের মনে থাকবে। কবি হিসেবে পরিচিত জগমোহন দিল্লিকে দুর্গে পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে প্রায়ই কবিতা লিখতেন। তিনিই সঞ্জয়ের অনুপ্রেরণায় গরিব মানুষকে সাফাই করে বুলডোজার চালিয়ে শহরকে সুন্দর করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। অসহায় মানুষজন সেদিন সবার প্রথম রুকসানা সুলতানার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। সঞ্জয়-ঘনিষ্ঠ রুকসানা তখন নিজের এলাকায় নির্বীজকরণ চালাচ্ছেন। রুকসানা সাহায্য তো করলেনই না, অসহায় মানুষদের কাছ থেকে নির্বীজকরণ করা যাবে এমন পুরুষের তালিকা চাইলেন। রাস্তায় সেদিন পুলিশ, আধাসেনা নেমেছিল। আশ্রয় খুঁজতে থাকা দুহাজার মানুষকে মারধর করা, ধর্ষণ করা, ছিনতাই করা, কোনও কিছুই বাদ থাকেনি। ৮৪০টি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কেউ বলেন সে দিন ৬ জন (জগমোহনের ভাষ্য) মারা গিয়েছিল, কেউ বলেন ১৬০০ জন।
স্বৈরাচারকে একটা নান্দনিক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জয়। সেই ব্যাটনই হাতে তুলে নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। হিন্দু রাষ্ট্রকে নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ গড়ে তোলার জন্য যে নগর পরিকল্পনা তিনি করেছেন তার কাছে সঞ্জয় নেহাতই বামন। সঞ্জয় বড়জোর চাইতেন শহরটাকে নতুন করে দেওয়াল দিয়ে ঘিরতে। আর মোদির উচ্চাকাঙ্ক্ষা গোটা শহরটাকে নতুন করে গড়ার। যখন স্বাস্থ্য পরিষেবা না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন তখন মোদির ধ্যান-জ্ঞান সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রোজেক্ট। শোনা যাচ্ছে, এমন ভাবেই এই সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরি করা হবে যাতে রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন অন্যান্য প্রশাসনিক দফতরগুলো প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকেই দেখা যায়। এর থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যদি সুযোগ থাকত তাহলে গোটা দেশটাই নতুন করে গড়তে প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই আমরা দেখে ফেলেছি বেনারস ঘাটের 'সৌন্দর্যায়ন' বা আমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামের নব নামকরণ। এগুলি সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশবিশেষ।
সঞ্জয় কার্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গে ধৈর্য্য রেখে সমঝোতা করতেন। মানুষকে চমকে দেওয়াই ছিল তাঁর কৌশল। আসলে তিনি এ ব্যাপারে অন্তত মাকেই অনুসরণ করতেন। তাঁর মা জনতা কল্পনাও করতে পারবেন না এমন বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। অনেকের হয়তো স্মরণে থাকবে না ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ (জুলাই ১৯৬৯) এবং প্রিভি পার্স বিলুপ্তিকরণ ঘোষণা (সেপ্টেম্বর ১৯৭০) ইন্দিরা করেছিলেন হঠাৎ। সেই পথ অবলম্বন করেই নির্বাচনী গণতন্ত্রকে মোদি সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচারের দিকে নিয়ে গিয়েছেন এবং জনমত না নিয়েই বারংবার নানা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন। এ দেশে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে যে ভাবে কৃষি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তা সংসদের মর্যাদাকেই খাটো করে। এই আইন কার্যকর হলে যারা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকছে,ঘোষণার আগে তাদের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। ফলে এসব দেখেশুনে বুঝতে হয়, মোদির শাসনধারাটি সিদ্ধান্তবাদী। ২০১৬ সালে নোটবন্দি, ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ, ২০২০ সালের ২৪ মার্চ হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা, এই তিনটি উদাহরণ তাঁর চরিত্রকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট।
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার চিরাচরিত নিয়ম গুলিকে অবমাননা করেই মোদি তাঁর ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। চকিত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ইমেজ তৈরি করতে পেরেছেন যা একজন সাধারন রাজনীতিবিদের 'দিচ্ছি-দেব' প্রতিশ্রুতির অনেক ঊর্ধ্বে। চাপ দেওয়া, সমঝোতা করা, দাবিদাওয়া আদায়ের নির্বাচনী রাজনীতির যে চিরাচরিত স্তম্ভগুলি, সেগুলিকে ভেঙে ফেলেছেন নরেন্দ্র মোদি। এই ধরনের অনুপ্রেরণামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই তাঁর নেতৃত্বের প্রতি এক ধরনের ভক্তিবাদের জোয়ার এনেছে, যুক্তির আতস কাচের তলায় ফেলে তার মতামতকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা কমেছে। এই ধরনের আকস্মিক সিদ্ধান্ত জনগণকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে দেয় এবং গণতন্ত্রে জবাবদিহির যে দায়বদ্ধতাটুকু স্বীকৃত তাকেও লঘুতর করে তোলে। কার্যক্ষেত্রে হয়েছে তাইই।
জরুরি অবস্থার সঙ্গে মোদি সরকার পরিচালনার পার্থক্য এই যে মোদি একটি স্বৈরতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থাকে নির্বাচন কমিশন-সহ কিছু মুক্ত সংস্থাকে সামনে রেখে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। আমরা মনে রাখব যদি আরএসএসের আদর্শগত জোরালো ভিত্তিটি না থাকত তবে এমনটা করা সম্ভব হতো না। অন্য দিকে জরুরি অবস্থা আইন প্রয়োগ করেই চাপিয়ে দিয়েছিল ইন্দিরার কর্তৃত্ববাদী সরকার। মোদি সরকারের প্রাণবায়ু হলো ভক্তি। এই ভক্তির ছলাৎছল শব্দ শোনা যেত না হিন্দুত্বের দ্বিতীয় ইঞ্জিন ছাড়া।
হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা এমন একটি রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করতে চায় যেখানে কোনও রকম সমালোচনা সহ্য করা হবে না। অন্য দিকে ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ শত্রু চিহ্নিত করার কাজ চলবে যাতে হিন্দু রাষ্ট্রের সম্প্রীতি বিপন্ন এই ধারণাটি তৈরি করে আরো সংহতির বোধ তৈরি করা যায়। কাজেই ক্ষমতা দখলের জন্য এ ক্ষেত্রে সব সময় টার্গেট হবে মুসলিম জনগোষ্ঠী। যে সব কার্যকলাপ এই হিন্দুরাষ্ট্রে বৈধ তা নাগরিক সহিংসতার আর গণহত্যার মাঝে একটি ধূসর রেখায় বিচরণ করে। এসব বিচার করেই আমরা বলতে পারি যে, জরুরি অবস্থার রাষ্ট্রীয় সহিংসতাই ক্রমে হিন্দুত্ববাদী নাগরিক সহিংসতায় অভিযোজিত হয়েছে। হিন্দুত্বের অবশ্য একটি শত্রু নয়, শত্রু তালিকায় রয়েছেন খ্রিস্টানরা, বামপন্থীরা, যে কোনও নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী সংগঠন বা কোনও বিরোধী দলনেতা। এমনকি তিনি বা সেই দল হয়তো কখনও বিজেপির শরিক থাকলেও। এর মধ্যে শিবসেনা, শিরোমণি অকালি দল, জম্মু-কাশ্মীর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস সবই রয়েছে। ৩৭০ ধারা রদ করার সময় পিডিপি মুখ্যমন্ত্রী (একসময়ে তিনিও বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন) মেহেবুবা মুফতি-সহ বহু নেতাকেই গৃহবন্দি করে রেখেছিল বিজেপি। অর্থাৎ এই নতুন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটাই নিউ নর্মাল যে রাষ্ট্র ক্ষণে ক্ষণে অভ্যন্তরীণ শত্রু চিহ্নিত করে জাতীয়তাবাদের জিগির ছড়িয়ে দেবে। আর অন্য দিকে ক্রমেই একটি ভক্তির কাঠামো তৈরি করবে। ভক্তি সেই সমস্ত হিন্দু নেতাকে যারা রাজনীতি এবং সমাজকে হিন্দুত্বকরণের পথে ক্রমে নিয়ে যাবে।
এই নেতৃত্বের করিশ্মা আর আদর্শের এত গভীর ভিত্তি জরুরি অবস্থার সময় ছিল না। সে সময় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে মূল চাবিকাঠি ছিল ইন্দিরা এবং তাঁর পুত্রের ব্যক্তিত্ব। দেশ এগোচ্ছে, এই শ্লোগান দিয়ে শূন্যতাকে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন ইন্দিরা সঞ্জয় জুটি। আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। ভক্তিতে ডুবুডুবু শান্তিপুর। তবে এ কথাও ঠিক, করোনা অতিমারীতে কুশাসনের কারণে বহু নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু আজ অনেক ভক্তের ঘুম ভাঙিয়েছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন নেতৃত্বের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণে সমস্যার জায়গাটা ঠিক কী। তবে জরুরি অবস্থার সময় যেমনটা হয়েছিল, এ ক্ষেত্রে রাতারাতি এই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সমস্যাটা সরিয়ে ফেলা যাবে না। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন, ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছিল ক্ষতচিহ্ন। আর এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন হয়েছে একটি গভীর আদর্শ থেকে, তাকে এক কথায় মুছে ফেলা অসম্ভব।
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা সেদিন দেখেছিলাম গণতন্ত্রহীনতা কী ভাবে ছাত্রদের জীবনে, তাদের আচরণে প্রভাব ফেলেছিল। আমরা এই জরুরি অবস্থার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ এই দেশের প্রবীণ নাগরিক হিসেবে আমরা অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি আমাদের ছেলেমেয়েরা কী ভাবে এই আদর্শগত বাতাবরণের সঙ্গে সমঝোতা করবে! যে দেশকে আমরা বিশ্বের সবথেকে বড় গণতন্ত্র হিসেবে চিনতাম জানতাম সেই দেশই যেন বধ্যভূমি। আমাদের গণতন্ত্রের অহংকারই একদা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক স্তম্ভগুলোকে শক্তিশালী করেছে। সেই আমরাই আজ আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান।